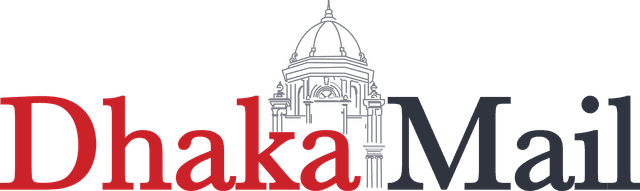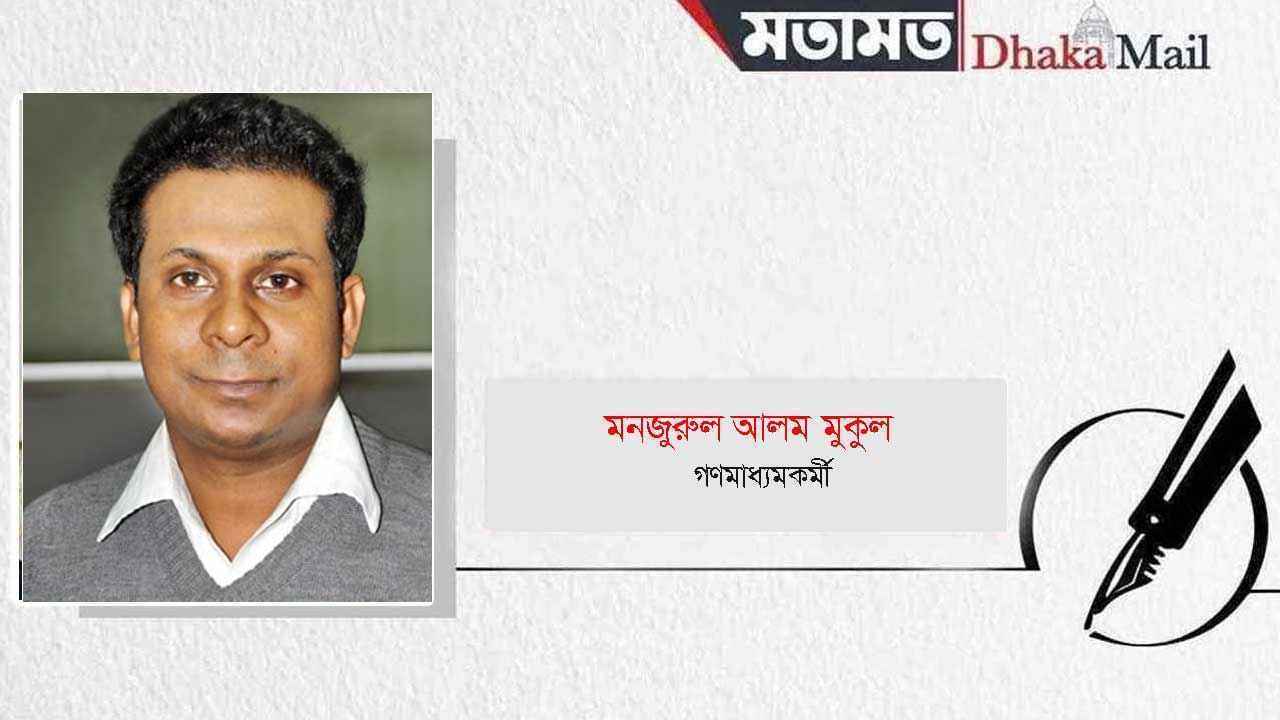“স্বাধীনতা তুমি পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল। স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি। স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।’’
কবি শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতায় এমন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্বাধীনতার প্রকৃত বা আসল রূপ উপলব্ধি কিছুটা করা যায়। হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বিশ্বের বুকে স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল এদেশের মানুষ। এই দিন আমাদের কাছে যেমন গৌরবদীপ্ত, চিরস্মরণীয় ও অনন্য সাধারণ দিন তেমনি এক তীব্র বেদনারও বটে। কেননা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ও অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছিল এই স্বাধীনতা। আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের আশায় এ দেশের লাখ লাখ মানুষ সেদিন তাদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়েছিল।
বিজ্ঞাপন
রক্ত ঝরানো যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে আমরা সেই রক্তঋণ যেন পরিশোধ করতে পারছি না। বার বার ভঙ্গ হয়েছে সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। স্বাধীনতার সুফল পাওয়ার জন্য ২০২৪ সালেও আবার রক্ত ঝরল। যে কারণে স্বাধীনতার ৫৪তম দিবসে আত্মসমীক্ষার অনেক বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
আমাদের পরাধীনতা বা অন্যের দ্বারা শোষিত হওয়ার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ছিল। এ ইতিহাস এদেশের মানুষ যেন ভুলে যেতে বসেছে। বিশ্ব মোড়ল ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো যেন আমাদের ওপর চেপে বসতে চাইছে। নিজ ভূমিতে থেকেও আমাদের প্রতিদিন দেখতে হয় অন্যের চোখ রাঙানি।
বাংলাদেশ নিয়ে বিদেশিদের কলকাঠি নাড়ানো ও মাথা ঘামানো যেন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে। একে অপরকে শায়েস্তা করার জন্য, ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতা থেকে কাউকে সরানোর জন্য বিদেশিদের সঙ্গে হাত মেলানো যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি জাতীয় স্বার্থ।
বাংলাদেশের ক্ষমতা বদলের হাত যেন এদেশের মানুষের হাতে নেই, সবাই চেয়ে থেকে বিদেশিদের ওপর। বিদেশ থেকে একটা ফর্মুলা বা সিস্টেম আসে আর তারপর সেই মোড়কে আটকানো হয় এদেশের জনগণকে।
বিজ্ঞাপন
বিদেশিদের হস্তক্ষেপ, পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় কিছু হলে তাদের স্বার্থটাই গুরুত্ব পাবে, আমাদেরটা নয়। প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের স্বার্থ আছে বলেই আমাদের পাশে এসে কেউ রোহিঙ্গার মতো বড় সমস্যার সমাধানে কেউ সাহায্য করল না।
বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ও অন্য কিছু মোড়ল রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী মহল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একের পর এক কার্যক্রম ও মনগড়া মন্তব্য শুধু আপত্তিকরই নয়, আমাদের কতটা দুর্বল ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে সেটাও উপলব্ধির বিষয়। এমনকি মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার থেকে আরাকান আর্মির মত সংগঠনও বাংলাদেশকে তাচ্ছিল্য করে চলেছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে ভারতে সফররত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড যে মন্তব্য করছেন তা বাংলাদেশের জন্য চরম সুনামহানির সামিল। অন্যদিকে ঢাকা সফরে থাকা মার্কিন সিনেটর গ্যারি চার্লস পিটার্স বললেন, এই বিষয়ে বিশাল মিথ্যা তথ্যের কিছু অংশ তাদের দেশে পৌঁছেছে। আসলে বাংলাদেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমন কিছু আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়।
অন্যদিকে ভারতের এক শ্রেণির মিডিয়া ও ব্যক্তি বাংলাদেশ সম্পর্কে অস্বাভাবিক আচরণ করেই চলেছে। বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিদিন যতসব আজগুবি গল্প প্রচারের আসর খুলে বসেছে। বাংলাদেশে নাকি ব্যাপক বিশৃঙ্খলা চলছে, প্রতিদিন ব্যাপক প্রাণহানি ঘটছে, বাড়ির বাইরে বের হলে মানুষ খুন-খারাবির শিকার হচ্ছে, সবকিছু লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হলে আর রেহাই নেই, সবাই পালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। এমন ধরনের খবর সাধারণ ভারতীয়দের মাথা গরম করে দিচ্ছে আর নীতিনির্ধারণী মহলকে বাধ্য করেছে কেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।
ভারতীয় গণমাধ্যমের বিষয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এডলফ হিটলারের সরকারের তথ্যমন্ত্রী পল জোসেফ গোয়েবলসের তত্ত্বের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ‘একটি মিথ্যা বার বার বললে সেটা সত্য হয়ে’। সে সময় কিছু বুদ্ধিজীবী, কবি ও সাংবাদিকও টাকার বিনিময়ে হিটলারের পক্ষে প্রচার চালাতেন। কিন্তু, মিথ্যা তো মিথ্যাই। একসময় সত্য বের হয়ে আসে, ছাইচাপা আগুনের মতো।
রিউমার স্ক্যানারের অনুসন্ধানে ভারতীয় গণমাধ্যমের বাংলাদেশ সম্পর্কিত অনেক খবর ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে একের পর এক অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বাস্তবতাবিবর্জিত প্রতিবেদন ও ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে চলেছে।
সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি সারা উপমহাদেশব্যাপী কমবেশি বিরাজমান। বিশেষ কারণে যদি কোনো ত্রুটি দেখা যায় তাহলে সবার উচিত কোনো প্রকার না উস্কে সমাধানে এগিয়ে আসা। তাছাড়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে?
বিজেপি সরকারের আমলেই সংখ্যালঘুদের দমনের জন্য অনেক আইন ও নীতি গৃহীত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত কোনো সরকার সংখ্যালঘুদের দমনের জন্য বিশেষ কোনো আইন করেনি ও নীতি গ্রহণ করেনি। তারপরও কেন এই অপপ্রচার?
ভারতের উচিত বাংলাদেশের এই বিশেষ সময় পছন্দের কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে এককভাবে সমর্থন না করে স্থিতিশীল বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করা।
বিষয়টি আমরা প্রায় অনেকেই জানি, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূকৌশলগত স্থানে অবস্থিত। স্থলপথে এশিয়ার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে বাংলাদেশই হলো সহজতম পথ। বঙ্গোপসাগর অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। অনেকের কাছে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকারের জন্য বাংলাদেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কারোর অবস্থান থাকলে ভারত মহাসাগর এলাকায়ও প্রভাব রাখতে পারে। বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো ছাড়াও আঞ্চলিক রাষ্ট্র গুলোর আলাদা আলাদা স্বার্থ রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাপারে তারা আগ্রহী ও কোনো না কোনো ভূমিকা রাখে।
ভৌগলিক দৃশ্যপট ও অন্যান্য বিবেচনায় এই ভূখণ্ডের সমস্যা নতুন কোনো বিষয় নয়, অনেক পূর্বের। অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সীমান্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। গবেষকদের মতে, যত গোলমাল, সমস্যা ও নিরাপত্তাহীনতা সীমান্তে বা বর্ডারে। সীমান্তবর্তী সমাজে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সবসময় একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে থাকে এবং বাংলা কোনো সময় বিষয়টি থেকে বের হতে পারেনি।
উত্তর ও পূর্বে পর্বতমালা ও দক্ষিণে সাগরে ঘেরা অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ছিল বিভিন্ন শাসকদের শেষ সীমান্ত। বাংলা যেমন আর্যদের শেষ গন্তব্য তেমনি আফগান-তুর্কি-মোঙ্গলসহ মুসলিম শাসকদেরও শেষ গন্তব্য। গবেষকরা সীমান্তকে বিরোধ অর্থেও বিবেচনা করেন। বাস্তবক্ষেত্রে বাংলায় অনেক সীমান্ত ও বিরোধ বিদ্যমান ছিল এবং সাধারণভাবে সবকিছু পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ধাবিত হয়ে ছিল।
ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিরোধ ছাড়াও ছিল সাংস্কৃতিক বিরোধ। আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় বা অনার্যদের সঙ্গে। তারপর আবার বৌদ্ধবাদ ও ইসলামি সংস্কৃতি। এটা একটা কৃষিজও সীমান্ত। বেশিরভাগ যেমন সমতল ও সমপ্রকৃতির ভূমি ও কৃষি, তবে পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে আলাদা।
দেশে ঘটনার পর ঘটনা নতুন কিছু নয়, যে কারণে হয়ত সুদূর অতীতকাল থেকে এই প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত ‘বাংলা হলো বালঘাকখানা’ অর্থাৎ গোলযোগের আবাসভূমি। আর এই জন্য শুধু বহিরাগত বা বিদেশিরা দায়ী এমনটা নয়, আমাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোও কোনো অংশে কম দায়ী নয়।
বাংলার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে অনেকে অনেক তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা দিয়েছেন মন্তব্য করেছেন। তবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব, কাঠামোবদ্ধ বা দার্শনিক ধারণা যা-ই বলুন, সেটা প্রথমে এসেছিল ১৫৭৯ সালে মোঘল সম্রাট আকবরের প্রধান উপদেষ্টা আবুল ফজল আল্লামির কাছে থেকে।
প্রায় ৫০০ বছর আগে আবুল ফজলের অবাক করা কথাগুলো ঘিরেই যেন আজও বাংলার রাজনীতি পরিচালিত হয়।
বিচক্ষণ আবুল ফজল আগে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতেন এবং সবকিছুই একজন ভালো পর্যবেক্ষকের মতো যৌক্তিক চোখে দেখতেন। জানা যায়, মোঘল সাম্রাজ্যের ১২টি প্রদেশের অন্যতম বাংলায় না এসে বাংলার অনেক তথ্য-প্রমাণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে এ সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যায় তিনি উপনীত হন। আবুল ফজল আল্লামা লিখেছিলেন, ‘বাংলা নামের দেশটি এমন একটি অঞ্চল, যেখানে আবহাওয়ার কারণে অসন্তোষের ধুলা সবসময় উড়তেই থাকে। মানুষের শয়তানিতে এখানকার পরিবার ও জনপদগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।’
আবুল ফজলের মতে, স্নায়ু বিকলকারী আবহাওয়া মানুষকে কলুষিত করে ও কলুষিত মানুষ সার্বভৌম শাসনকে ধ্বংস করে। যে কারণে বহিরাগতদের ব-দ্বীপকে শক্তিশালী হওয়ার পথ সুগম করে। বাংলায় এমন পরিবেশ বিদ্যমান থাকে যেখানে কেউ গেলে বা যারা বসবাস করে, স্বাভাবিকভাবে সবাই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।
স্থানীয়দের (বাঙালি) মধ্যে সহজে বিভেদ সৃষ্টি হয়। নিজেদের স্বার্থের বিষয়টি সবার কাছে প্রধান থাকে। ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সার্বভৌম শাসন ও সবার জন্য মঙ্গলকর (জাতীয় স্বার্থ) বিষয়সমূহ ধ্বংস করা তাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। এ কারণে তিনি লিখেছিলেন ‘এদের স্বার্থ দেখিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কর আর সুবিধা নাও।’
আবুল ফজল সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিনব তত্ত্বটি শুধু দিয়েই যাননি, মোঘলরা অক্ষরে অক্ষরে তার বাস্তবায়ন করে এবং সফলতা পায়।
বাংলার মানুষের অধঃপতনের এই অভিনব তত্ত্বটি ব্রিটিশ, ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি সবাই জানত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিক কর্মকর্তারা এই তত্ত্বটি জোরালোভাবে গ্রহণ করেছিল। রবার্ট ক্লাইভ জেনেশুনে বা তত্ত্বটি ভালোভাবে রপ্ত করে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিল। পরিবেশ সবই বিদ্যমান ছিল, তিনি শুধু খেলাটা চালিয়ে গিয়েছিলেন। ক্লাইভ এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, চক্রান্তের ফল নিশ্চিত।
১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, পলাশী যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের মাত্র ৩২০০ সৈন্যের কাছে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৫০ হাজারের চৌকস বাহিনীর অভাবনীয় পরাজয় ঘটে। আর ইংরেজরা প্রায় দুশো বছর এর সফল বাস্তবায়ন করে গেছে। এই ধারা পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত থাকে।
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়লেও নতুন করে বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদের নীতি। বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর অনেকে প্রকাশ্যে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আর অনেকে কৌশলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ ও আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কৌশলের একটি নীতি হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে সুযোগ বুঝে রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ যেন এই ধরনের চক্রান্তের মধ্যে না থাকে সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
এমন অবস্থায় দেশকে স্থিতিশীল, ঐক্যবদ্ধ, টেকসই ও শক্তিশালী করতে কার্যকর ও আসল গণতন্ত্রের খুবই প্রয়োজন ছিল। নির্দিষ্ট সময় পরপর সুষ্ঠু নির্বাচন আর ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা ভালো পরিবেশ আবশ্যক। বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব-সহিংসতা-অসন্তোষ-অরাজকতা-অস্থিতিশীলতা কাম্য নয়। এগুলো বারবার ঘটতে বা চলতে থাকলে একটা দেশ ধীরে ধীরে একটি সংঘাতময় ও অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকেই চলে যায় এবং অন্যরা সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
পাকিস্তান আমল থেকে এদেশে সুগঠিত গণতন্ত্রের কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। পাকিস্তান আমলে একটা বিতর্ক ছিল ইসলাম নাকি গণতন্ত্র। ধর্মের নাম করে গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। শেষ কি হল, ধর্মের কোনো উপকারও হলো না, আবার গণতন্ত্রও হলো না। গণতন্ত্র যদি কিছুটা থাকত তাহলে অন্তত ধর্মের কিছুটা উপকার হতো।
জোরজুলুম করে ক্ষমতায় থাকাকে ইসলাম সমর্থন করে না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হলেও সংবিধান আসে ১৯৫৬ সালে এবং প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে যেটা শেষ পর্যন্ত ৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়।
মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র সেই পূর্বের শনির দশা থেকে বের হতে পারিনি। স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হলো। চেপে বসল সমাজতন্ত্রের ভূত। নিষিদ্ধ হলো সব রাজনৈতিক দল, চালু হলো বাকশাল। একপর্যায়ে গণতন্ত্রও হলো না, সমাজতন্ত্রও হলো না। এভাবেই দেশে একপর্যায়ে চালু হলো নিয়ন্ত্রিত বা সিস্টেমের গণতন্ত্র।
এরশাদ সরকারের পতনের পর ধারণা করা হয়েছিল, এদেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। ১৯৯১, ১৯৯৬ (১২ জুন), ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন মোটামুটি ভালোই হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া পরপর তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল বিরোধীদের নির্বাচনে আনতে না পারা। জোর যার মুল্লুক তার—এই প্রবাদবাক্যই হয়ে উঠেছে আমাদের গণতন্ত্রের এক ধরনের সংজ্ঞা।
গণতন্ত্র মানে শুধু ভোটের আয়োজন করা নয়, গণতন্ত্রের অন্য সব বৈশিষ্ট্যগুলো যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র হয় না। ভিন্ন ভিন্ন মত, বহুকণ্ঠ, বিতর্ক গণতান্ত্রিক রীতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা বিরুদ্ধ মতের স্বীকৃতি দিতে চায় না এবং তর্ক-বিতর্ক কোন মতেই মেনে নিতে চায় না।
হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি একে অপরকে উচ্ছেদ করার অপচেষ্টার মতো এমন কিছু ঢুকে পড়েছে যা শুধু গণতান্ত্রিক পরিসরকে খর্বই করছে। আর স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান না গড়ে, সুস্থ গণতন্ত্র চর্চা না করে, দেশে অসন্তোষ রেখে উন্নয়ন করলে তা কখনও টেকসই হয় না। জনতার বিক্ষোভের প্রবল আঘাতে এক সময় তাসের ঘরের মত ভেস্তে যায়, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
আমাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো বদলানোর পথ যে একেবারে বন্ধ, এমনটাও নয়। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার, ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সার্বভৌম শাসন, সবার জন্য মঙ্গলকর ও জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এ দেশের মানুষ আসলে কী জন্য বা উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সেই মর্মার্থ উপলব্ধি করা এখন সময়ের দাবি।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী