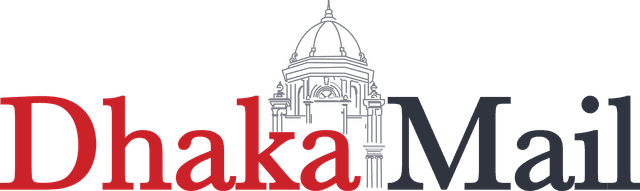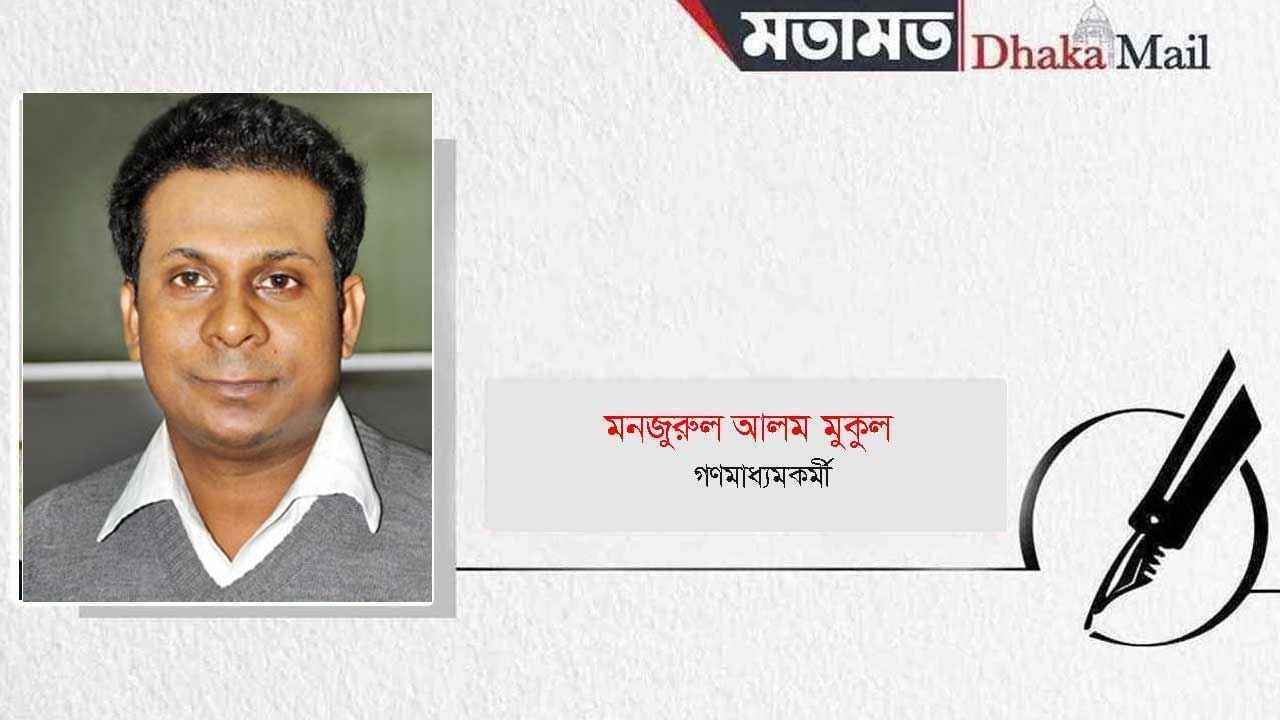ভাষা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, ভাব তৈরি ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। এই ভাষার জন্মের পেছনে রয়েছে অপার রহস্য। পৃথিবীর জীবিত-মৃত সব ভাষার আদি উৎস আফ্রিকা। অতি প্রাচীনকাল থেকে আফ্রিকার এই মানুষ জীবিকা, বেঁচে থাকা বা অন্য বিশেষ কিছু কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক সময় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন ধরনের ভাষার উদ্ভব হয়। আর ভাষাগুলোকেই কেন্দ্র করে মানুষের সৃষ্টিশীল রূপগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি।
বাংলা অঞ্চলের ভৌগলিক পরিবেশ, জলবায়ু, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাংলা ভাষা। আর এই ভাষাভাষী মানুষের সৃষ্টিশীল রূপ নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলা সংস্কৃতি। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রণালী, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের সাথে জড়িত যন্ত্রপাতি, নিয়মনীতি, আচারঅনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সব ধরনের ধরনের ঐতিহ্য প্রভৃতি হয়ে ওঠে সংস্কৃতির উপাদান। তাইতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের দেশি খাবার, কুলা, ঢেঁকি, নাঙ্গল, দুবলা ঘাস, কলাগাছ, আমপাতা ইত্যাদি সব কিছু।
বিজ্ঞাপন
বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উৎসব উৎযাপন আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এটি একটি স্থানীয় ও সর্বজনীন উৎসব। যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মিলিতভাবে পালন করে আসছে। এই উৎসবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কোনও রং নেই তবুও প্রতিবারই চলে কোন না কোন রং লাগানোর অপচেষ্টা, দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখা। আর এ সবগুলো চলে কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে। কখনও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আবার কখনও আমাদের ভূখণ্ডের বাইরে।
ভারতের বিজিপি সরকার অনেক দিন ধরে সে দেশের সব কিছুতে একটা ধার্মিকীকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তারা লেগেছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। বিষয়টি লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের হয়রানির শিকার হতে হয়, এমনকি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেখার অপচেষ্টা চালানো হয়। এনআরসি, ডিটেকশন ক্যাম্প, পুশব্যাক ও জেল-জরিমানার মত ঘটনার শিকার হতে হয়।
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে গেরুয়া বাহিনী বাংলা সন প্রবর্তনের ইতিহাস পরিবর্তনের এক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গাব্দ সূচনার কৃতিত্ব থেকে মোগল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ও টোডরমলকে সরিয়ে সপ্তম শতাব্দীর গৌরাধিপতি শশাঙ্কে করতে চায়। ইতিহাসে এর পাথুরে প্রমাণ না থাকলেও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ও পালন করছে নানা কর্মসূচি।

বিজ্ঞাপন
আকবরের সময়ে প্রচলিত রাজকীয় সন হিজরি চন্দ্রসন হওয়ায় প্রতি বছর একই মাসে খাজনা আদায় সম্ভব হত না। তাছাড়া ঐ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বর্ষপঞ্জি প্রচলিত ছিল যেমন- বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, লক্ষণাব্দ, ফার্সি পঞ্জিকা, আমনি মন, বিলায়িতি অব্দ, মল্লাব্দ ইত্যাদি। রাজস্ব আদায়ের শৃঙ্খলার জন্য আকবরের নির্দেশে তার বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন টোডরমল একটি অভিন্ন বর্ষপঞ্জি প্রচলন করেন যা ফসলি সন বা বাংলা সন নামে পরিচিত। এটি শুরু হয়েছিল ১৫৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে। তবে শুরুর দিন কিন্তু প্রথম তথা ১ সাল ছিল না, ছিল ৯৬৩ সাল। অর্থাৎ হিজরি চন্দ্র সনকে ফসলি সৌর সনে রূপান্তরিত করেন। এ বিষয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, ‘শশাঙ্ক তাঁর নিজের রাজত্বকালে তাম্রশাসনে অন্তত পাঁচটি নিষ্কর ভূদান করেছিলেন। তিনি যদি অব্দ জারি করেই থাকবেন, তা হলে তো এই দানে সেই অব্দের উল্লেখ থাকত! কিন্তু কোথাও তা নেই। এমনকি তাঁর অধীনস্থ রাজাদের ভূসম্পদ দানের ক্ষেত্রেও গুপ্তাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।’
সম্রাট আকবরকেই বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইতিহাসবিদ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তক অমর্ত্য সেন প্রমুখ একমত। অতএব বিজিপির এই দাবি সম্পূর্ণ অমূলক।
বিজিপির দাবি আকবর বা টোডরমল কখনও বাংলায় আসেনি। কিন্তু বাংলায় আসা বা না আসার প্রশ্ন কোন বিষয় হতে পারেনা। ইতিহাসে স্বীকৃত যে, মোগলদের নীতি ও পদক্ষেপের কারণে বাংলার আর্থিক-সামাজিক চারিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া সন শব্দটি আরবি আর সাল শব্দটি ফার্সি। অতএব, বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে যে মুসলিম সুলতান বা সম্রাটদের সম্পর্ক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের কেউ কেউ মনে করে পহেলা বৈশাখ পালন ও বাংলা সংস্কৃতির অনেক কিছুর কারণে ধর্মের ক্ষতি হতে পারে। তাদের ধারণা ছিল বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে এবং এই সংস্কৃতিও অন্য কিছু। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে অনেক কিছু ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ল্যাটিন ভাষা থেকে ইতালীয়, স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষার উদ্ভব। এই ব্যাখ্যার আলোকে সাধারণীকরণ করা হয় সংস্কৃত থেকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষা এসেছে। তবে আধুনিক গবেষণায় এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলার উদ্ভব হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ভাষার মত বাংলার স্বতন্ত্র ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বরং উর্দু আর হিন্দি ভাই ভাই ভাষা। উর্দু আর হিন্দি দুটি ভাষাই সংস্কৃতির অপভ্রংশ খাড়িবুলি থেকে উৎপন্ন। শব্দ, অর্থ, ভাষার উৎস ও ধরন একই। উর্দু লেখা হয়ে আরবি লিপিতে আর হিন্দি লেখা দেবনাগরী লিপিতে।
ভাষা গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি বা সূচনাকালে এদেশে আর্য ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। যে কারণে বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ এসেছে। অন্যদিকে, বাংলা ভাষার সুগঠিত রূপ বা বিকাশ শুরু হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের দিকে এবং এই সময় শুরু হয় মুসলিম শাসন। মিশতে থাকে ফার্সি-আরবি শব্দ। রীতিমত পারস্যকরণ বলা যেতে পারে। ১৯৬৬ সালে শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালি ফার্সি উৎসের ৯ হাজারের বেশি বাংলা শব্দ ও অভিব্যক্তির একটি অভিধান প্রকাশ করেন। এদেশে এসেছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের ভাষার অসংখ্য শব্দ মিশেছে বাংলা ভাষায়।
মূলকথা, বাংলার নিভৃত পল্লীতে আমাদের যে পূর্ব-পুরুষরা বাস করত, তাদের নিজেদের শব্দগুলোর সাথে সাথে অন্যদের থেকে কিছু কিছু নিয়ে বাংলা ভাষা তৈরির কাজ শুরু করেছিল। বলা যেতে পারে বাংলা একক কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়। বাংলায় স্থানীয় অনার্য জনগোষ্ঠী বা আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথমে কেউ হিন্দু বা মুসলমান ছিল না। এক সময় তাদের কেউ হিন্দু হয়, কেউ মুসলমান। আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে এসেছে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি।
নিজে কী, নিজের পরিচয় কী হওয়া উচিত— এমন চিন্তা এ দেশের মানুষ খুব কমই করেছে। এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও এ মাটি ও তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিজের মনে করতে সবসময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও হীনমন্যতায় ভুগেছে। আত্মপরিচিতির এই সঙ্কট নতুন কিছু নয়। এক সময় হিন্দু সমাজব্যবস্থায় লক্ষণীয় ছিল, যারা উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যারা কনৌজ-মিথিলা বা উত্তর ভারত থেকে এসেছে, এমন ভাব যারা দেখাতে পারত, তারাই ছিল সমাজে বেশি সম্মানিত।
আর মুসলিম সমাজে ভাবখানা এমন ছিল ঐ যে গানে আছে, ‘ইরান-তুরান (মধ্য এশিয়া) পার হয়ে এসেছি’। মুসলিমরা নিজেদের ইরান-তুরান–আরব-বাগদাদের পীর-ফকির, রাজাবর্গ ও তাদের অনুচর ও সিপাহীদের বংশধর প্রমাণে মহাব্যস্ত ছিল। তবে, সম্প্রতিকালে হাড়গোড় ও অন্যান্য আধুনিক নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, এদেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর। বাইরের জনগোষ্ঠীর তাদের খুব কমই মিল রয়েছে।
অরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক রিচার্ড মাক্সওয়েল ইটন গবেষণায় প্রমাণ করেছে মুসলমানদের ৫০০ বছর শাসনের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে শেষ ১০০ বছরে অর্থাৎ মুঘল আমলে। এর পূর্বে মুসলিম জনসংখ্যা কোন সময় ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি কোন সময় ছিল না। বিশেষ করে আকবরের সময় বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে যখন বদ্বীপের পাললিক সমতলের, নিভৃত পল্লির সুবিপুল পিছিয়ে পড়া স্থানীয় দরিদ্র লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা শুরু করে। আর এটা সম্ভব হয়েছিল সেই সময় আসা মুসলমানদের কারণে যাদেরকে আমরা সূফী-সাধক বা ধর্ম প্রচারক বলে থাকি।
রিচার্ড এম ইটনের মতে, খ্রিষ্টান ধর্ম কখনো ইউরোপে বিকশিত হত না, যদি না তা ইউরোপের স্থানীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে না নিত। ইসলাম ও বাংলার ক্ষেত্রে এটা কম সত্য নয়। তার মতে, ধর্ম যদি সামজের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারে তবে তা শুধু জাদুঘরে বা পুস্তকে টিকে থাকে। ইসলাম সেই সময় বাংলার ভূমি ও স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ায়ে নিয়ে ছিল। স্থানীয়রাও ইসলামকে নিজেদের আপন করে নিয়ে ছিল।
বহিরাগত বা তাদের বংশধরদের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী বেড়েছে ঠিকই; তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। পূর্বে যেসব বহিরাগত মুসলিমরা এসেছিল তারা ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। পুরনো রাজধানীগুলোর চারদিকে জড়ো হয়ে বা অন্যান্য নগর ও তার আশপাশে তারা বসবাস করত। তারা প্রত্যন্ত গ্রামে যেত না এবং পেশা হিসাবে কৃষি ছিল তাদের অপছন্দের।
এটা ইতিহাস স্বীকৃত যে, বাংলায় শাসন কার্য, ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের জন্য বহিরাগতরা এসেছে। তবে বাংলা এতই দুর্গম ও সুযোগসুবিধা এতই কম ছিল যে অনেকে চাকরি ও ব্যবসা শেষে নিজেদের দেশে ফিরে যেত। এমনটা জানা যায়, মোঘল আমলে যারা রাষ্ট্রীয়কাজে বাংলায় এসেছিল তাদের বেশ কষ্টেই দিন কাটাতো। ইংরেজদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল ‘টু রেইন্স’ (two rains) অর্থাৎ রোগ বালাই আর প্রতিকূল পরিবেশের কারণে এক বর্ষাকাল পার করে দ্বিতীয় বর্ষাকাল দেখার সৌভাগ্য অনেকের হতো না।
আর বহিরাগতরা যারা বাংলায় থেকে গিয়েছিল তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারেনি। এক সময় নিজেরাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। উত্তর ভারত থেকে যেসব ব্রাহ্মণ বাংলায় এসেছিলেন তারা কেউ বউ বা স্ত্রী সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এমন শোনা যায় না। তেমনই ইরান, মধ্য এশিয়া, আরব ও উত্তর ভারত থেকে যেসব মুসলিমরা বাংলায় এসেছিলেন তারাও সবাই বউ বা স্ত্রী সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এমন তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে এখানেই ঘর সংসার শুরু করতেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বাংলায় যারা মা হয়েছে তারা সবাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ছিল। আর ভাষা ও সংস্কৃতিতে মায়েদের প্রভাব থেকেই যায়। আমরা মাতৃভাষা বলি, পিতৃভাষা বলি না।
আশা করা হয়েছিল ১৯৭১ সালের পর অন্য কিছু ভাবার প্রবণতা শেষ হবে, কিন্তু সেটা হয়নি। বিশেষ করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের চরিত্রে পরিবর্তন আসেনি। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কান্নাকাটি করলেও পরে গুরুত্বহীন হয়ে ওঠে। তাদের এখন ‘গরিবের ঘোড়া রোগ’ দেখা দিয়েছে। তাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশে বা অন্য কোনও দেশে বসবাস, ব্যবসা করা বা আসা-যাওয়া অনেক সম্মানের ও আভিজাত্যের ব্যাপার। আত্মপরিচয়ের এই সংকট তৈরি হয়েছে দেশের সম্পদ পাচার হওয়ার প্রবণতা। দুর্নীতি করে হোক আর সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে হোক বিদেশে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশে গড়ে উঠেছে বেগমপাড়ার মত অভিজাত এলাকা। যে সব এলাকায় এ দেশের সন্তানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।
ইংরেজরা এক সময় জাহাজ ভর্তি করে এদেশ থেকে ধনসম্পদ নিয়ে যেত। আর এখন আমরা নিজেরাই বহন করে তাদের দিয়ে আসছি। আমরা এখনও ঔপনিবেশিক মনজগতের মধ্যেই আছি। একে বলা যায় ‘Self colonization’ অর্থাৎ নিজেরাই দাসে পরিণত হওয়া।
অন্যদিকে কিছু লোকের ধর্মীয় অপব্যাখ্যাও কোন দিন টেকেনি। কেননা বর্তমানে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, তাদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারী, যা আরবের পর পৃথিবীর ২য় সর্বোচ্চ জনগোষ্ঠী। ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ভৌগোলিক অঞ্চল বা এলাকা, জীবনপ্রণালী বা উৎপাদন ব্যবস্থার, সংস্কৃতির, ভাষাভাষী ও খাদ্যাভ্যাসের লোক ইসলামের অনুসারী। প্রতিটি জনপদের মানুষ নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রেখে ইসলামের বিধান মেনে চলবে এটাই নিয়ম। আর পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, ‘আর তাঁর [আল্লাহর] নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ [সুরা রুম : আয়াত ২২]

পারস্য তথা ইরানে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে নওরোজ উৎসব ব্যাপক জাঁকজমকভাবে পালিত হয়। শুধু ইরান নয় ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, তাজিকিস্থানসহ অনেক দেশের মুসলমানেরাও এটা পালন করে। প্রাচীন পারস্যের পরাক্রমশালী সম্রাট জমশীদ খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালে নওরোজ প্রবর্তন করেছিল। অনেকের মতে নওরোজ একটি জরথুস্ত্রবাদী উৎসব। তবুও ঐতিহ্যগত কারণে মুসলমানেরা এটি পালন করে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও জীবন প্রণালীর ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে অনেক উৎসব পালন করা হয় যেগুলোকে শরিয়তের অংশ করা হয়নি, কেননা সেগুলো ছিল স্থানীয়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরাও অনেক স্থানীয় উৎসব পালন করে।
বাংলায় যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী তাদের সাথে উত্তর ভারতের হিন্দুদের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। কেননা তারা বাংলার হওয়ায় উত্তর ভারতের সব কিছু গ্রহণ করতে পারেনি, এটাও আমাদের সংস্কৃতির একটা বড় প্রমাণ।
শোভাযাত্রা নিয়ে বিতর্ক
দল বেঁধে যাওয়া, মিছিল করে যাওয়া এ দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাইতো তারা দল বেঁধে ঈদগাহে যায়, পূজার অনুষ্ঠানে যায়, বিয়েসহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যায়। শিয়া মুসলমানেরা আশুরার দিনে তাজিয়া মিছিল বের করে। পহেলা বৈশাখের দিনে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ নিয়ে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি করে আসছে। এবার ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’ নামকরণ করা হয়েছে। এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও মতের লোক রয়েছে, অতএব সবাই একইভাবে পহেলা বৈশাখ ও শোভাযাত্রা পালন করবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। বাংলায় যা আছে, যাদের দেখা যায় তাদের ছবি নিয়ে এ দেশের মানুষ মিছিল করতে পারে সেটাই স্বাভাবিক।
অনেকের মতে, মঙ্গল মূলত দ্রাবিড়দের শব্দ যা বাংলা ভাষার পৈতৃক। কেউ কেউ মনে করে, এটি ফার্সি শব্দ, মঙ্গল থেকে মোঘল হয়েছে। আবার অনেকের মতে, এটি সংস্কৃত বা আর্যদের শব্দ যেখানে রয়েছে ধর্মের গন্ধ। অন্য দিকে আনন্দও একটি সংস্কৃত শব্দ। মঙ্গল শব্দটির যে দোষ দেওয়া হয় আনন্দ শব্দটিও কি সে দোষের বাইরে নয়? আসলে শব্দ একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বিষয়গুলো আরও জটিল হয়ে যায়। ভারতের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের একটি উক্তি আছে, ‘মোদি সরকার সবই পাল্টাচ্ছেন, তবে হিন্দু শব্দটা কি পাল্টাতে পারবেন, কেননা এটা আরবদের শব্দ।’
এ পর্যন্ত শোনা যায়নি কেউ পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গিয়ে শিরক করেছে। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গিয়ে কেউ কোনো দিন বলেনি ‘আরেকজন সৃষ্টিকর্তা আছে’। তাছাড়া অশ্লীলতা ও অসামাজিক কাজের জন্য কি উৎসবের দোষ দেওয়া যাবে?
কে কীভাবে পহেলা বৈশাখ পালন করছে, এটা আমাদের দেশের মূল সমস্যা নয়। সুস্থ গণতন্ত্র চর্চা ও ন্যায় বিচারের অভাব, দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচার আমাদের প্রধান সমস্যা। তাছাড়া আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। ভিন্ন ভিন্ন মত, কণ্ঠ, দ্বন্দ্ব-বিতর্ক গণতান্ত্রিক রীতির মধ্যে পড়ে।
মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাপক। অনেকের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এখন বিপন্ন। এমনও পূর্বাভাস আছে, আগামীতে বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এমন স্থানে পৌঁছাবে যে পৃথিবীর অনেক সীমানা উঠে যাবে, সব মানুষ একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে, একইভাবে সবকিছু চিন্তা করবে। অদূর ভবিষ্যতে এই মহামারি থেকে আমাদের সংস্কৃতি কতটা টিকে থাকবে সেটাই বিবেচনার বিষয়।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী