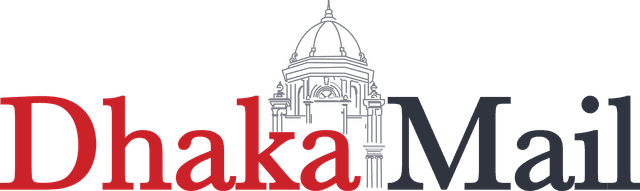ভারতের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি এখন গভীর সংকটে। একের পর এক দেশ ভারতের ওপর থেকে আস্থা হারাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এক সময় নেতৃত্ব দেওয়া ভারত এখন প্রায় একা হয়ে পড়েছে। বন্ধুর চেয়ে নিয়ন্ত্রক হওয়ার চেষ্টা ভারতকে কূটনৈতিকভাবে বিপদে ফেলেছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের কারণে দেশটির কূটনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।
নেপাল: বন্ধুত্ব হারিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে
আঞ্চলিক যে কয়টি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে তার মধ্যে একটি নেপাল। দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, ভারত ও নেপালের মধ্যে এখন দৃশ্যমান দূরত্ব তৈরি হয়েছে। একসময় নেপাল ভারতের নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিল। সীমান্ত, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বন্ধন—সবদিক থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক ছিল অটুট। কিন্তু গত এক দশকে সেই সম্পর্কের গভীর চিত্র বদলে গেছে। ভারত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেপাল এখন চীনের দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ছে।
বিজ্ঞাপন
এই টানাপোড়েনের সূচনা ২০১৫ সালে, যখন নেপাল তাদের নতুন সংবিধান ঘোষণা করে। সংবিধানে কিছু ধারা নিয়ে ভারতের আপত্তি ছিল। বিশেষ করে ভারতের সীমান্তবর্তী তেরাই অঞ্চলের মধেসি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ইস্যুতে ভারত প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানায়। এরপরই ভারত ‘অঘোষিত’ সীমান্ত অবরোধ শুরু করে, যা নেপালে গভীর সংকট তৈরি করে।
ভারতের অবরোধের ফলে নেপালে জ্বালানি, ওষুধ ও খাদ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশজুড়ে ভারতবিরোধী ক্ষোভ দানা বাঁধে। বহু শহরে ভারতবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই ভারতকে আর বন্ধু নয়, নিয়ন্ত্রক বা বাধা হিসেবে দেখতে শুরু করে নেপালিরা।
এই অবস্থায় চীনকে কৌশলগতভাবে কাছে টেনে নেয় কাঠমান্ডু। চীন এই সুযোগে নেপালে রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য খাতে বড় আকারের বিনিয়োগ শুরু করে। চীন-নেপালের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য রুট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাশাপাশি সামরিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কেও চীন ও নেপালের আলোচনা এগোয়।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও খারাপ হয় ২০২০ সালে। সে বছর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিপুলেখ সীমান্ত দিয়ে একটি সড়ক উদ্বোধন করেন, যা নেপাল নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। এর প্রতিক্রিয়ায় নেপাল পার্লামেন্টে একটি নতুন মানচিত্র অনুমোদন করে, যেখানে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা এলাকাকে নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়। ভারতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, নেপাল সেই মানচিত্র কার্যকর করে।
বিজ্ঞাপন

ওই ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে সাময়িক সংলাপ হলেও সম্পর্ক আর আগের জায়গায় ফেরেনি। নেপাল এখন পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য চায়। তারা ভারতের একচ্ছত্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করছে। চীনের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ (BRI)-এ নেপালের যুক্ত হওয়া এবং চীনা প্রকল্পে অংশগ্রহণ, ভারতের জন্য কৌশলগত উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।
দ্যা ডিপ্লোম্যাটের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়— নেপাল-চীন ব্যবসায়িক ফোরামে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি বলেন, ‘আমাদের বন্ধু চীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছে। তার অগ্রগতি দেখে সারা বিশ্ব অবাক হয়েছে।’
পরবর্তীতে বেইজিংয়ে চীনে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘আমি আবার চীনে এসেছি। আমাদের দুই দেশের মধ্যে গভীর আস্থা ও বোঝাপড়া রয়েছে। নতুন যুগে নেপাল-চীন সম্পর্কের জন্য আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছি।’
বিশ্লেষকরা বলছেন, নেপাল আর ভারতের ‘ছায়াতলে’ থাকতে চায় না। তারা স্বাবলম্বী এবং বহুমুখী কূটনীতি চায়, যেখানে চীনের মতো শক্তিধর প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি, সীমান্ত নিয়ে আগ্রাসী অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা—এসবই দুই দেশের সম্পর্ককে ঠেলে দিয়েছে শীতলতার দিকে।
ভুটান: ঐতিহাসিক সম্পর্কেও চীনের ছায়া
এদিকে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, ভুটান ও ভারতের মধ্যে এখন স্পষ্ট দূরত্বের আভাস মিলছে। ভুটান এক সময় ভারতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। ১৯৪৯ সালে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যার আওতায় ভুটান তার পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের পরামর্শ নিত। ২০০৭ সালে এই চুক্তি সংশোধন করে ভুটানকে কৌশলগত কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হলেও, ভারতের প্রভাব থেকেই যায়।
তবে সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে ভুটানের অবস্থান। বিগত এক দশকে দেশটি ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে চীনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলছে। চীন ও ভুটানের মধ্যে সীমান্তবিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ শুরু হয় ২০২১ সালে। ওই বছর দুই দেশ একটি তিন-ধাপের রোডম্যাপ চুক্তিতে পৌঁছায়, যা ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ভুটান-চীন সীমান্ত-সংক্রান্ত বিরোধের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো ডোকলাম এলাকা—যেটি ভারতের কৌশলগত সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২০১৭ সালে এই ডোকলাম অঞ্চলেই ভারত ও চীনের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। চীন সেখানে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করলে, ভুটানের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ভারত সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু সেই সময়ের পর থেকে ভুটান এই ইস্যুতে অনেকটাই নীরব ভূমিকা পালন করছে। ভুটান আর আগের মতো সরাসরি ভারতের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে না।

চীন এ সুযোগে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় গতি এনেছে। তারা সীমান্তবিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে ভুটানকে কাছে টানছে। যদিও এখনো ভুটানের সঙ্গে চীনের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক হয়নি, তবে আলোচনার গতি বলছে—সেদিকেই এগোচ্ছে পরিস্থিতি।
এমন প্রেক্ষাপটে ভারত বেশ কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা চাইছে ভুটান যেন চীনের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তিতে না যায়, যা ভারতের কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী হয়। বিশেষ করে ডোকলাম ইস্যুতে ভুটান যদি চীনের সঙ্গে সমঝোতায় যায় এবং ওই অঞ্চলের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে ভারতের ‘সিলিগুড়ি করিডোর’ বা ‘চিকেন নেক’ নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।
ভারত এখনও ভুটানকে বড় অঙ্কের সাহায্য ও অনুদান দিয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ভুটান এখন আর আগের মতো ভারতনির্ভর নয়। তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে। চীন ও ভারতের মধ্যে কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষা করে নিজেদের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে থিম্পু।
মালদ্বীপ: ‘ইন্ডিয়া আউট’ বাস্তবতা
দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপেও এখন স্পষ্ট ‘ইন্ডিয়া আউট’ বাস্তবতা বিরাজ করছে। এক সময় ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত মালদ্বীপ এখন সে সম্পর্ক থেকে সরে আসছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতবিরোধী স্লোগান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতির এই দৃশ্যমান বদল ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে গভীর টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে।
মূলত ২০২৩ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোহাম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পর এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়। তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় খোলাখুলি ‘ইন্ডিয়া আউট’ স্লোগান ব্যবহার করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, মালদ্বীপে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তার বিজয়ের পর সেই প্রক্রিয়া শুরুও হয়।
ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম—মালদ্বীপে ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি। ভারতের সহায়তায় একটি সামরিক ঘাঁটি পরিচালিত হওয়া এবং ড্রোনসহ কিছু সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা মোতায়েনের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছিল। মালদ্বীপের একটি বড় জনগোষ্ঠীর অভিযোগ, ভারত এই দ্বীপরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।
এছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রকল্প ও সহায়তার নামে দেশটির ওপর প্রভাব বিস্তার, স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং সরকারের সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটানোর ধারণা জনগণের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবিতে ‘ইন্ডিয়া আউট’ আন্দোলন শুরু করে। সামাজিক মাধ্যমে এই স্লোগান ভাইরাল হয়ে ওঠে।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, মোহাম্মদ মুইজ্জুর সরকারের প্রধান কূটনৈতিক পদক্ষেপই ছিল ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপ ছাড়ার ঘোষণা। ২০২৪ সালের শুরুতে এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে ভারত রাজি হয় সেনা সরিয়ে নিতে। এই সিদ্ধান্ত মালদ্বীপের রাজনীতিতে ব্যাপক সমর্থন পায়।
এর মধ্যেই, মালদ্বীপের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক জোরদার হয়। চীন দেশটিতে অবকাঠামো, পর্যটন ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে শুরু করে। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু বেইজিং সফর করেছেন এবং চীনের সঙ্গে নতুন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, মালদ্বীপ এখন ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি চায়। তারা আর শুধু ভারতের ওপর নির্ভর করতে চায় না। বরং বিকল্প শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী। ফলে ‘ইন্ডিয়া আউট’ কেবল একটি রাজনৈতিক স্লোগান নয়—এটি দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক বাস্তবতায় ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।
শ্রীলঙ্কা: পুরনো অবিশ্বাস, নতুন চ্যালেঞ্জ
দীর্ঘদিনের পুরনো সম্পর্ক থাকলেও ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগে এখন আড়ষ্টতা স্পষ্ট। রাজনৈতিক অনাস্থা, অর্থনৈতিক প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং চীনের প্রভাব—সব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।
শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই স্পর্শকাতর। ১৯৮০–৯০ দশকে তামিল সমস্যা নিয়ে ভারত যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা আজও শ্রীলঙ্কার একাংশে নেতিবাচক প্রভাব রেখে গেছে। এলটিটিই (তামিল টাইগার) বিদ্রোহ দমনে ভারতের হস্তক্ষেপ, ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড—এই সব ইতিহাস দুই দেশের পারস্পরিক আস্থায় ফাটল ধরিয়েছিল।
সেই ফাটল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মুছে গেলেও, নতুন চাপে এখন সম্পর্ক আবারও টানাপোড়েনে। সবচেয়ে বড় সংকট শুরু হয় ২০২২ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময়। দেশটিতে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানিসংকট ও ঋণখেলাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তড়িঘড়ি কিছু অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা আরও বড় সাহায্যের আশায় ছিল, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ছাড় ও বিনিয়োগের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলেই দেশটির অনেকের মত।

অন্যদিকে, চীন এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে। বিপুল পরিমাণ ঋণ ও বিনিয়োগ দিয়ে চীন শ্রীলঙ্কার অবকাঠামো উন্নয়নে যুক্ত হয়। হাম্বানটোটা বন্দর, কলম্বো পোর্ট সিটি প্রকল্পসহ অনেক বড় চীনা প্রকল্প দেশটিতে চালু হয়েছে। চীনের এই প্রভাব ভারতকে কৌশলগতভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।
তবে এখানেই শেষ নয়। ২০২৩ সালের দিকে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে একাধিকবার চীনের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। একইসঙ্গে চীন থেকে সামরিক জাহাজ ও প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়। এই সব কিছু ভারতের জন্য স্পষ্ট বার্তা—শ্রীলঙ্কা আর শুধু ভারতের দিকে তাকিয়ে নেই।
শুধু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নয়, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ভারতবিরোধী আবেগ ব্যবহার করা হয়। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য থেকে প্রভাবিত হয়ে শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে তামিল জনগোষ্ঠীর মাঝে কিছুটা সন্দেহ বা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, একদিকে ভারতের পুরনো ইতিহাসের জটিলতা, অন্যদিকে চীনের কৌশলগত আগ্রাসন এবং শ্রীলঙ্কার বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতি—এই তিনটি কারণেই ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক এখন কঠিন পরীক্ষার মুখে।
বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক: দীর্ঘকালের বন্ধুতা এখন ঝুঁকিতে
বাংলাদেশ একসময় ভারতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। কিন্তু এখন দুই দেশের সম্পর্ক গভীর অনাস্থায় ভরপুর। গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনা সরকারের একচেটিয়া সমর্থক হিসেবে ভারত ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও ভারতের সুবিধা হয়েছে অনেক, কিন্তু বাংলাদেশের পেতে হয়েছে সীমান্তে নাগরিকদের একের পর এক লাশ।
১৯৭২ সালে দুই দেশ একটি বাণিজ্য চুক্তি করে। তাতে ১৬ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে পণ্য পরিবহনের ট্রানজিট সুবিধা চালু হয়। তবে এই সুবিধার বিপরীতে বাংলাদেশের লাভ খুব কম। বরং ভারত একতরফা বাণিজ্য সুবিধা নিয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে চলছে।
রাজনৈতিকভাবে ভারতের প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে গোপন কিছু চুক্তির মাধ্যমে ভারত এখানে হস্তক্ষেপ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সহায়তা বাংলাদেশকে দুর্বল করেছে। কিছু চুক্তি ও সমঝোতায় ভারতের লাভ বেশি হয়েছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মনে করে, তারা ভারতের কাছ থেকে বড় কোনো উপকার পায়নি। তিস্তা চুক্তি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। বর্ষাকালে ভারত হঠাৎ পানি ছেড়ে দেয়। শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকে রাখায় বাংলাদেশে খরা ও ভয়াবহ বন্যার ঘটনা ঘটে। সীমান্তে বাংলাদেশিদের ওপর হত্যাকাণ্ডও বন্ধ হয়নি।
সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভারত বড় প্রভাব বিস্তার করছে। ভারতের টিভি চ্যানেল ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো চ্যানেল ভারতে দেখা যায় না। অনেকেই এটাকে ‘সাংস্কৃতিক আগ্রাসন’ বলছেন।
ট্রানজিট ইস্যুতে ভারত ৭টি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে সংযোগের জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করছে। এই ব্যবহারে বাংলাদেশের লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশি হচ্ছে। রাস্তা ও পরিবেশের অবনতি ঘটছে।
বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দাপট বেড়েছে। বিশেষ করে আদানি গ্রুপের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ নানা প্রকল্পে পরিবেশগত বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।
এসব কারণে দুই দেশের সম্পর্ক এখন শীতলতায় ভরপুর। এই শীতলতাকে হিম শীতল পর্যায়ে নিয়ে গেছে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান। ওই অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ভারতের পুতুল সরকারের পতন ঘটেছে। এরপর আওয়ামী লীগের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় নিতে হয়েছে দিল্লিতে। যা কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে।
আফগানিস্তান: তালেবানের উত্থানে ভারত পিছিয়ে
আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের প্রত্যাবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও ছিন্নপ্রায়। একসময় কাবুলে শক্তিশালী প্রভাব থাকা ভারত এখন অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তালেবানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখনও স্পষ্ট নয়, বরং দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থানই প্রকট।
২০০১ সালে তালেবান সরকার উৎখাতের পর আফগানিস্তানে ভারত ছিল অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। সড়ক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও সংসদ ভবন নির্মাণসহ নানা অবকাঠামো উন্নয়নে ভারত বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করেছিল। আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বৃত্তি ও কূটনৈতিক সহায়তায়ও সক্রিয় ছিল নয়াদিল্লি।
কিন্তু ২০২১ সালে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান দ্রুত কাবুল দখল করে। এরপর থেকেই ভারত কার্যত আফগানিস্তান থেকে সরে দাঁড়ায়। তালেবানকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। ফলে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ ভেঙে পড়ে।
ভারতের শঙ্কা মূলত নিরাপত্তা ঘিরে। তালেবানের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আফগানিস্তানে হাক্কানি নেটওয়ার্ক ও লস্কর-ই-তৈয়বার মতো সংগঠনের অবস্থান—ভারতের জন্য উদ্বেগের বিষয়। কাশ্মীর ইস্যুতেও তালেবানের মন্তব্য ভারতের কূটনীতিকদের চিন্তায় ফেলে দেয়।

অন্যদিকে, তালেবান সরকার আফগানিস্তানে ভারতের বিনিয়োগ ও উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভারতের সাবেক ঘনিষ্ঠ অংশীদারদের অনেকেই তালেবান শাসনে কোণঠাসা। ফলে ভারতের কূটনৈতিক মূলধন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।
এই ফাঁকে চীন, পাকিস্তান, কাতার এবং ইরান তালেবান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। চীন ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে খনিজসম্পদ ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। পাকিস্তান বরাবরের মতো তালেবানের নীতিগত পৃষ্ঠপোষক, আর ইরানও প্রতিবেশী হিসেবে কৌশলগত যোগাযোগ ধরে রেখেছে।
তালেবান শাসনে নারী অধিকার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সমালোচনা থাকলেও, ভারতের ভূমিকা বরাবরই নীরব। একদিকে মানবিক সহায়তা পাঠানো হলেও, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক পরিকল্পনায় স্পষ্ট ঘাটতি রয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, ভারত বর্তমানে এমন এক অবস্থানে আছে, যেখানে আফগানিস্তানে তার কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কার্যত বন্ধ। তালেবানের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, আবার সম্পূর্ণ দূরে থেকেও কৌশলগতভাবে ঝুঁকিতে পড়ছে। এই দ্বিধান্বিত নীতিই ভারতকে আফগান ইস্যুতে পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভূরাজনীতিতে ভারতের প্রভাব অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানে এখন ভারতের কূটনীতি এক রকম অন্ধকারে—না এগোচ্ছে, না সরে আসছে।
মিয়ানমার-ভারত: জটিল সম্পর্ক
মিয়ানমার ও ভারতের সম্পর্ক একসময় ছিল কৌশলগত ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্মিত। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সম্পর্ক ক্রমেই জটিল ও অস্থির হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাজনিত নানা ইস্যু দুই দেশের দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। এই ঘটনার পর মিয়ানমারে শুরু হয় গণবিক্ষোভ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ। ভারত সরকার শুরুতে সতর্ক ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া জানায়, কিন্তু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে দিল্লি সামরিক জান্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রক্ষা করতে পারছে না।
অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতির জন্য মিয়ানমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড সীমান্ত মিয়ানমারের সঙ্গে মিলিত। এই এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোর ঘাঁটি রয়েছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে। অতীতে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় ভারত এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যে এই সহযোগিতা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এছাড়া, মিয়ানমারের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে জনমত ক্রমেই সমালোচনামুখর হচ্ছে। বিশেষ করে মিজোরামে বহু সংখ্যক মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা চীন ও জান্তাবিরোধী মানুষের আশ্রয় নেওয়ার ঘটনায় দিল্লির জন্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। দিল্লি আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে সীমান্ত রাজ্যগুলোতে অসন্তোষ বাড়ে; আবার মানবিক কারণে নরম হলে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে চাপ পড়ে।

বাণিজ্যিক ও অবকাঠামোগত দিকেও রয়েছে স্থবিরতা। ভারত-মিয়ানমার চীন-ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড সড়ক প্রকল্প, কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ প্রকল্পগুলো মিয়ানমারের অস্থিরতার কারণে ঝুলে গেছে। এতে ভারতের ‘অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি’ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
আরেকটি বড় পরিবর্তন এসেছে চীনের সক্রিয় ভূমিকায়। সেনা অভ্যুত্থানের পর পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারকে অনেকটা একঘরে করায় চীন সেখানে বিনিয়োগ ও কূটনৈতিক প্রভাব বাড়িয়েছে। ফলে মিয়ানমার এখন অনেক বেশি চীনমুখী। এতে ভারতের কৌশলগত প্রভাবও কমে গেছে।
সব মিলিয়ে, মানবিক, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক—এই চারটি ক্ষেত্রেই ভারত-মিয়ানমার সম্পর্ক এখন দ্বিধা ও অস্থিরতায় ভরা। সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন থাকলেও, বিশ্বাস ও কার্যকর সহযোগিতার অভাবে দুই দেশ এখন দূরত্বে ভুগছে। বিশেষ করে চীন যেভাবে মিয়ানমারে তাদের উপস্থিতি জোরদার করছে, তাতে ভারতীয় কূটনীতির জন্য এটা নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।
সার্ক: ভারতের নেতৃত্বে ব্যর্থতা
দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট সার্ক (SAARC) এক সময় আঞ্চলিক সংহতির প্রতীক ছিল। ১৯৮৫ সালে ভারতের নেতৃত্বে এই জোট গঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল—দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বাড়ানো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশাবাদ ফিকে হয়ে গেছে। আজ সার্ক কার্যত অচল। আর অনেকের মতে, এর মূল কারণ ভারতের নেতৃত্বের ব্যর্থতা।
সার্কের সদস্য দেশ আটটি—আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। কিন্তু জোটের সবচেয়ে বড় সদস্য ভারত অন্য দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। বরং ভারতের একক আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা, প্রতিবেশীদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, এবং দ্বিপক্ষীয় বিরোধ সার্ককে বারবার পেছনে ঠেলে দিয়েছে।
বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব সার্ককে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ২০১৬ সালে উরি হামলার পর ভারতের চাপে ইসলামাবাদে নির্ধারিত সার্ক সম্মেলন বাতিল হয়। তারপর থেকে আর কোনো শীর্ষ সম্মেলন হয়নি। ভারত সরাসরি পাকিস্তানের প্রতি আঙুল তোলে, অন্য সদস্যরাও ভারতের পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কৌশলে সার্ক ভেঙে পড়ে। দ্বিপাক্ষিক বিরোধ আঞ্চলিক জোটের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়।

এছাড়া সার্ককে কার্যকর করার চেয়ে ভারত বরং বিকল্প জোটগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়। বিমসটেক, আইওআরএ কিংবা কোয়াডের মতো কাঠামোয় ভারতের সক্রিয়তা অনেক বেশি। এতে করে সার্কের গুরুত্ব অনেকটা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ছোট দেশগুলো মনে করে, ভারত সার্ককে শুধু নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়, সমান অধিকার দেয় না।
বাণিজ্য সহযোগিতায়ও ভারতের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সার্ক ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (SAFTA) বাস্তবায়নে ভারত কার্যকর ভূমিকা রাখেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক বাণিজ্যে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, ভিসা নীতিতে কঠোরতা, এবং সীমান্তে নানা জটিলতা ছোট দেশগুলোর আস্থাহীনতা বাড়িয়েছে। তাদের ধারণা, ভারতের বাজারে ঢোকা কঠিন হলেও, ভারত তাদের বাজার দখল করে ফেলছে।
এদিকে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় বড় বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসায় অনেক সার্ক সদস্য এখন বিকল্প মিত্র খুঁজছে। ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক রেখে অনেকেই চীনের দিকে ঝুঁকছে। বিশেষ করে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ—এই তিন দেশ ভারতের নেতৃত্ব নিয়ে সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে একাধিকবার।
সবশেষে, আঞ্চলিক সংকট, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং নেতৃত্বের অভাবে সার্ক এখন প্রায় অকার্যকর। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্বের স্বপ্ন এখন প্রশ্নের মুখে। সার্ককে আবার সক্রিয় করতে হলে, শুধু বৈঠকের আয়োজন নয়—প্রয়োজন সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আস্থা ফেরানো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আস্থা ফিরিয়ে আনার পথটা খুব সহজ নয়।
কানাডা: হত্যাকাণ্ডে কূটনৈতিক বিপর্যয়
২০২৩ সালের জুনে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় সিখ সক্রিয় নেতা হারদীপ সিংহ নিজ্জারকে হত্যা করা হয়। কানাডা সরকারের অভিযোগ—এই হত্যাকাণ্ডে ভারতের সাথে সংযুক্ত সরকারি এজেন্টের ভূমিকা রয়েছে। কানাডার নিরাপত্তা সংস্থা সিএসআইএস বলেছে, এটি পররাষ্ট্রচাপের একটি ‘গুরুতর প্রকোপ’।
এ ঘটনার ঠিক পরেই কানাডা ভারতের উচ্চ আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিকে অবিরত ‘উদ্ধেস্থ’ হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারত কানাডার ছয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করে এবং পাশাপাশি ভিসা বন্ধ করে দেয়। প্রতিবাদ স্বরূপ ভারত ও কানাডা একে‑পরে অপরকে কূটনৈতিক প্রত্যাহারে চালায়।
ভারত–কানাডা সম্পর্ক এই হত্যাকাণ্ডের কারণে এতদূর পৌঁছেছে যে তখনকার কানাডা-প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডু অভিযোগ করেন, ‘ভারতীয় এজেন্টরা কানাডার স্থলে অপরাধে জড়িত’। ভারতের দৃষ্টি থেকে এটি ‘অকারণ’ ও ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।

২০২৪ সালের অক্টোবর নাগাদ কানাডা ৪১ কূটনীতিক ও তাদের পরিবারকে প্রত্যাহার করে ঘোষণা দেয় ‘উচ্চ সতর্কতা’। তখন থেকে ভিসার সেবা ধীর হয়ে যায়, কানাডা-ভ্রমণে সতর্কতা বাড়ে। ২০২৫ সালের জুনে, কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জি৭-শীর্ষ সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন। তারা দ্বিপক্ষীয় কূটনীতিক সম্মতি ও ট্রেড আলোচনা পুনরায় শুরু করার উদ্যোগে সায় দেন। কিন্তু কিন্তু সিএসআইএস আবারও সতর্ক করে, ‘ভারতের পাশাপাশি চীন, পাকিস্তান, ইরানও কানাডায় দমনমূলক পদক্ষেপ করছে’। ফলে জামজমাট কূটনৈতিক সংকট এখনও মুকুলে।
এই জটিলতার কিছু মূল কারণ
জাতীয় সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন: কানাডা মনে করে, ভারত নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও আইনী কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করেছে। দূতাবাস প্রত্যাহার: উভয় দেশ একমাত্র পদক্ষেপে শান্তিপূর্ণ কূটনীতির চালিয়ে দিতে পারছে না। বৈদেশিক গোষ্ঠীর প্রভাব: সিখ নির্বাসিতদের মধ্যে ‘খালিস্তান’ মতবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় ভারতের উদ্বেগের বিষয়। আন্তর্জাতিক চাপ: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কানাডার অবস্থানকে সমর্থন করেছে। ট্রেড ও ভিসা বাধা: দুই দেশের পুঁজিগত চুক্তি ও ভ্রমণ অবস্থা পুরোপুরি জটিল হয়ে পড়েছে।
নিজ্জার হত্যাসংঘটিত ঘটনায় কূটনৈতিক সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ রাজনীতির পারদ চূর্ণ করেছে। কানাডা ও ভারতের মধ্যে আস্থা–সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। যতক্ষণ তার-নামা নয়, দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হওয়া কঠিন। তবে স্বইচ্ছায় জি৭-সভায় দুই প্রধানের ঐকমত্য চিত্রে ছোট জোয়ারও দেখা গেল।
কাশ্মির নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপে ভারত
কাশ্মির ইস্যুতে ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। গত কয়েক বছরে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালের আগস্টে জম্মু-কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর থেকে বিশ্বমঞ্চে ভারতের সমালোচনা বেড়েছে। এতে অনেক দেশ কাশ্মির ইস্যুকে মানবাধিকার সংকট হিসেবে দেখছে এবং ভারতের নীতির বিরোধিতা করছে।
ভারত এই বিষয়টিকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সমস্যা হিসেবে ধরে নেয় এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করে। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মহল থেকে কাশ্মিরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। চীন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাশ্মির ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে ভারতের প্রতি চাপ বাড়াচ্ছে।

কাশ্মির সীমান্তে নিয়মিত সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষবিরতির ভঙ্গের ফলে উত্তেজনা কমছে না। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কও প্রভাবিত হয়েছে। এ অবস্থায় ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাশ্মির নিয়ে একাকীত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় নেতৃত্বের প্রভাব কমে যাচ্ছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, কাশ্মির ইস্যুতে ভারতের দ্বিপাক্ষীয় মনোভাব এবং শক্তিশালী কূটনৈতিক কৌশলের অভাবে দেশটি আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। যদি এই সংকট দ্রুত সমাধান না হয়, তবে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান আরো সংকুচিত হতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইরান: ভারসাম্যের পরীক্ষায় ভারত
ভারতের কূটনীতিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ভারসাম্যের কঠিন পরীক্ষার মুখে। এই তিন দেশের সঙ্গে ভারত দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তবে নানা কারণে এই সম্পর্ক এখন জটিলতার মধ্যে পড়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গত দশকে অনেক শক্তিশালী হয়েছে। দুই দেশ কৌশলগত, সামরিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তুলেছে। তবে বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। ভারতের পণ্য আমেরিকায় প্রবেশে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে আমেরিকার কিছু নিরাপত্তা নীতির সঙ্গে ভারতের স্বার্থ কখনও কখনও মিলছে না। এছাড়া, আমেরিকার চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ভারতকে সরাসরি যুক্ত করতে চাইছে, যা ভারতের ‘ব্যালেন্স অব পাওয়ার’ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই চাপ ভারতের জন্য কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন করে তুলেছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষ করে সামরিক ও মহাকাশ ক্ষেত্রে। ফ্রান্স ভারতের অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। তবুও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্রান্সের মানবাধিকার বিষয়ক উদ্বেগ এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছে। ফ্রান্স কখনও কখনও ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করায় সম্পর্ক নানাভাবে টানাপড়েনে পড়ছে।
ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘ ইতিহাসের। ইরান থেকে ভারত তেল আমদানিতে নির্ভরশীল। এছাড়া, দু’দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। কিন্তু পশ্চিমা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারতকে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় থাকতে হয়। আমেরিকার চাপের মুখে ভারতকে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বে ভারসাম্য বজায় রাখতে কঠোর কূটনৈতিক কাজ করতে হচ্ছে। এ কারণে ভারত-ইরানের সম্পর্ক প্রভাবিত হচ্ছে।
এই তিন শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে ফ্রান্স ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে কঠোর চেষ্টা করতে হয়। ভারতের এই ভারসাম্যহীনতার কারণে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট ও জটিলতা বাড়ছে। ভারতের বহুমুখী কূটনীতির ওপর এই চাপ ভবিষ্যতে তার আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও নিরাপত্তার জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।
এইউ